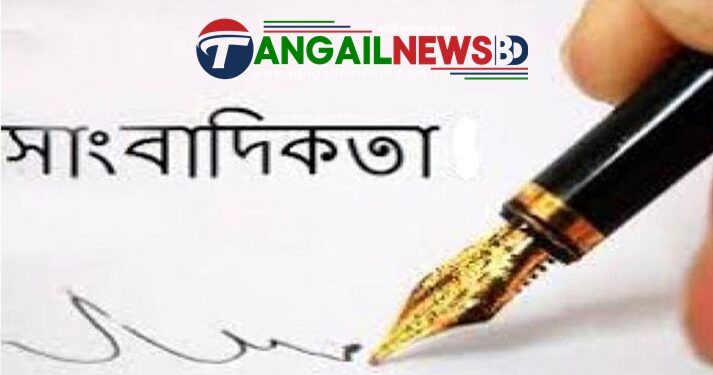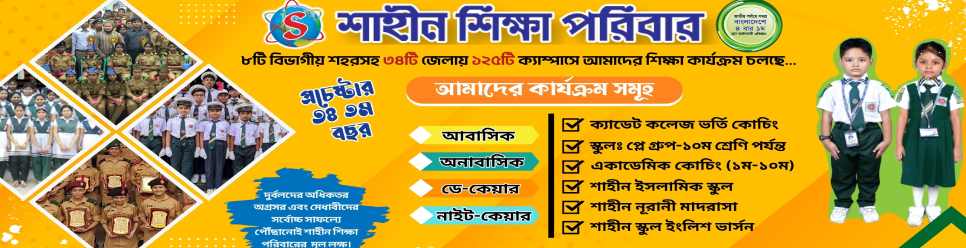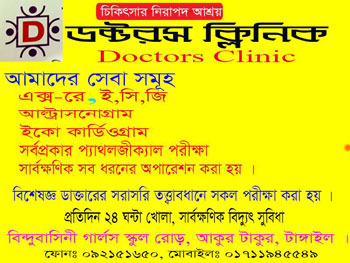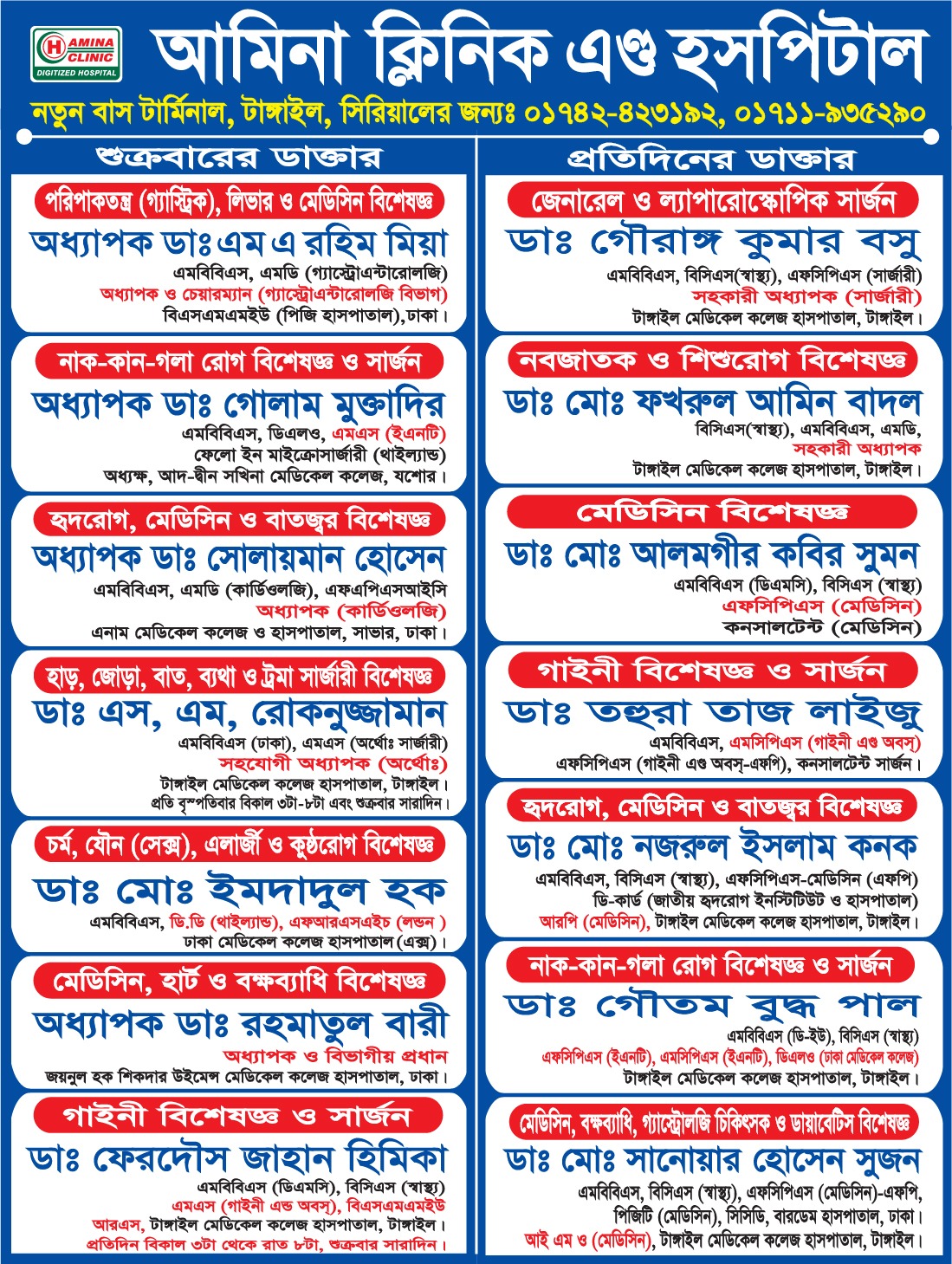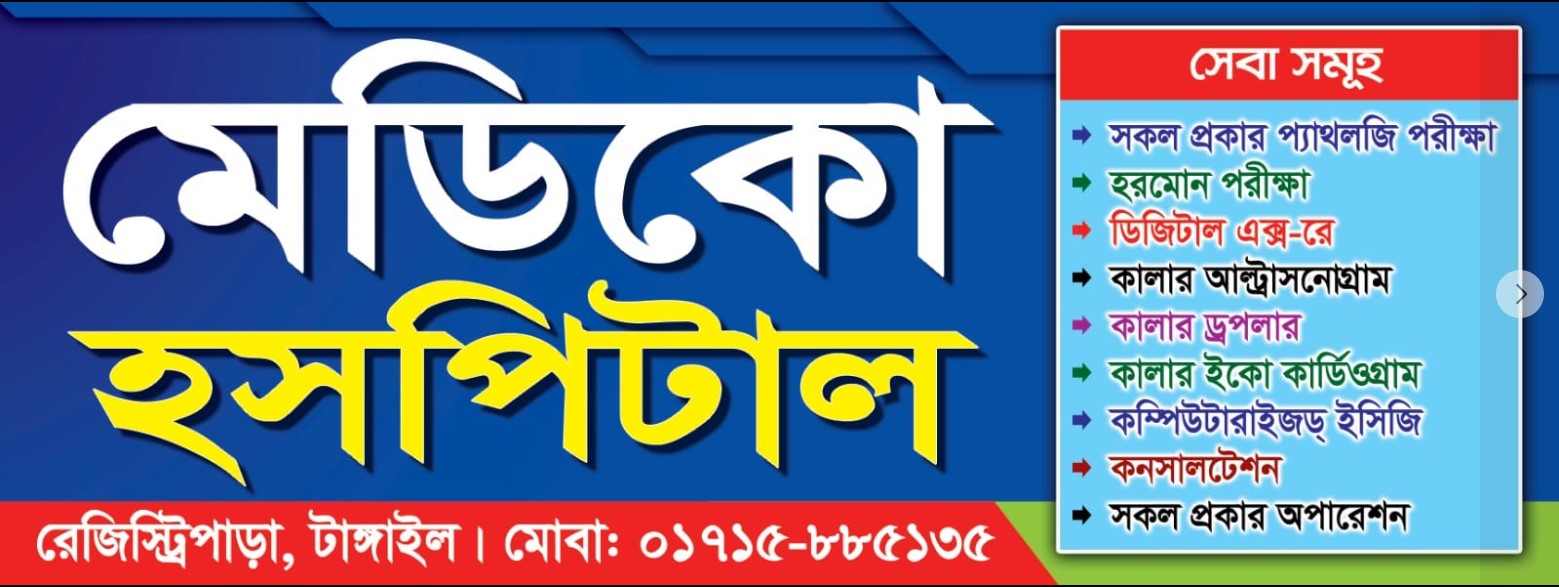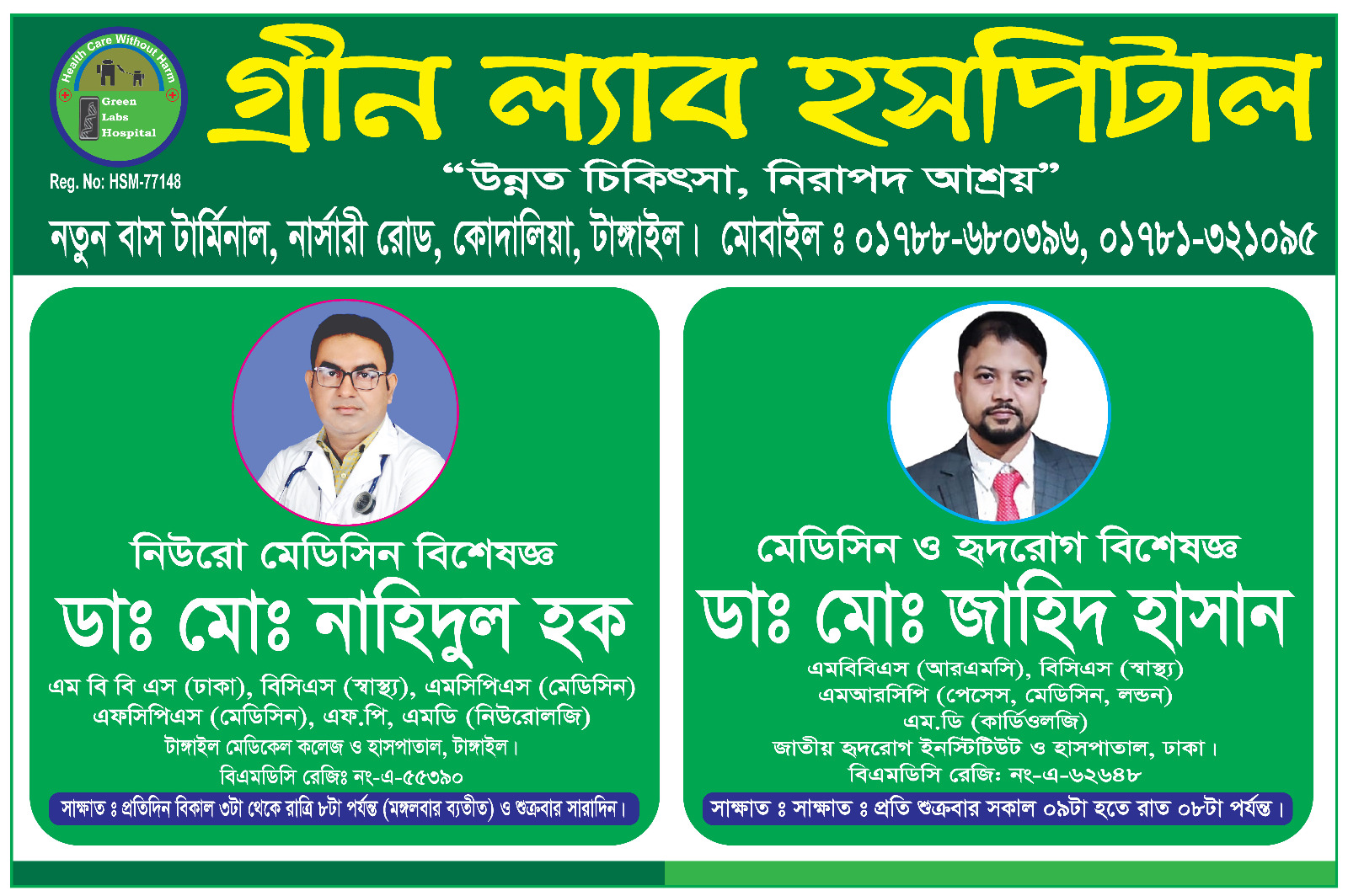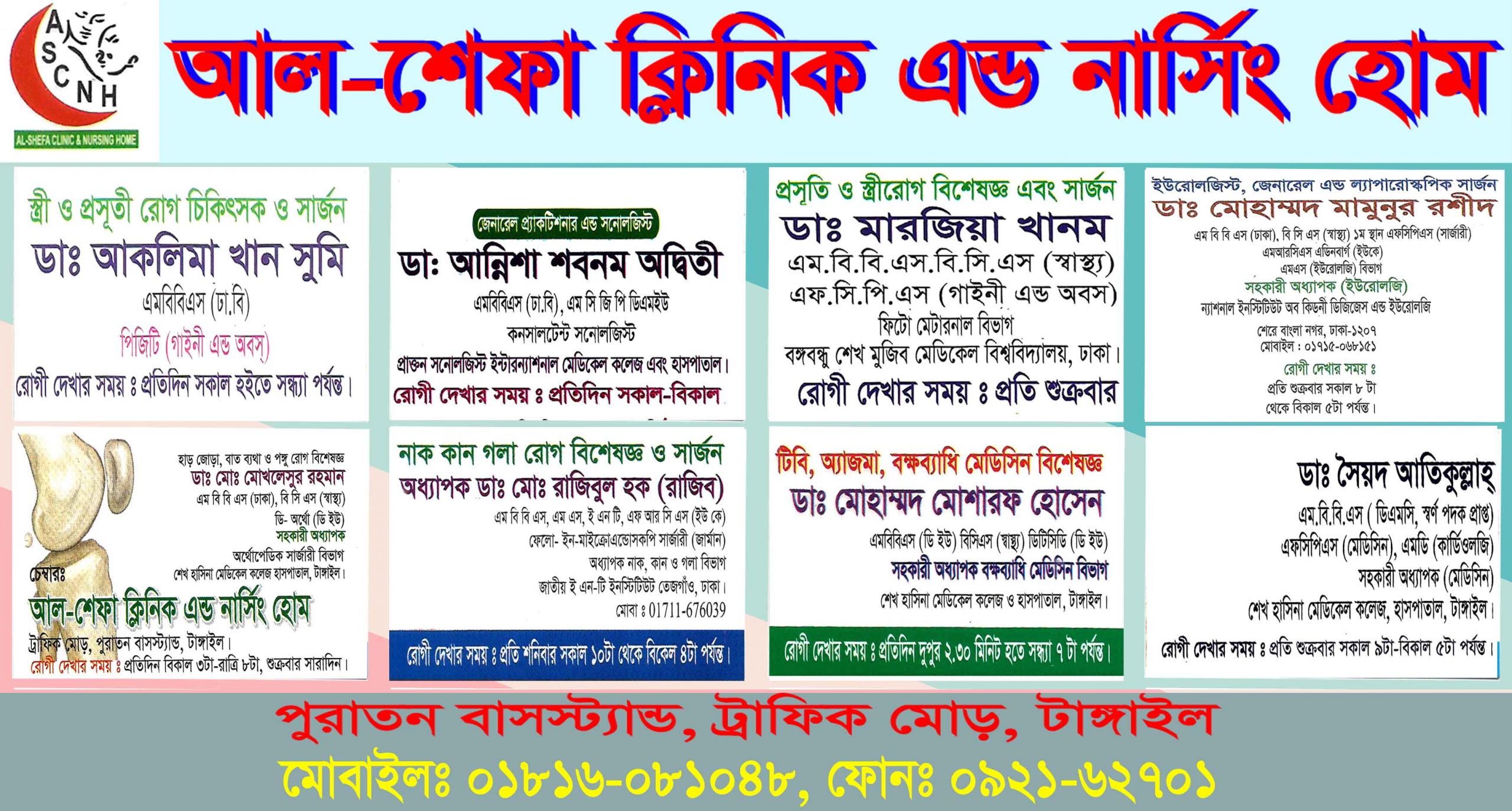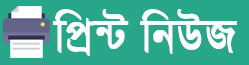
সাংবাদিকতাকে সমাজের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়। সাংবাদিকতা যুগে যুগে বিবর্তিত হয়েছে এবং বর্তমান যুগে প্রযুক্তির অগ্রগতি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসার এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের কারণে এর দৃশ্যপট ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এটি শুধু খবর পরিবেশনেই সীমাবদ্ধ নয়- বরং গণতন্ত্র রক্ষা, জনমত গঠন, এবং নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবর্তনশীল সাংবাদিকতা বিশেষ করে প্রযুক্তির বিকাশ এবং নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে বর্তমান বিশ্বে অতিদ্রুত রূপ পাল্টাচ্ছে।
সাংবাদিকতার সমসাময়িক চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সাংবাদিকতা একটি নতুন রূপ পেয়েছে। ডিজিটাল মিডিয়ার প্রসার সাংবাদিকতাকে আরও গতিশীল করে তুলেছে। এখন যেকোনো সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউব নাগরিক সাংবাদিকতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সাধারণ জনগণই এখন সরাসরি ঘটনাস্থল থেকে সংবাদ প্রচার করতে পারছে। এটা সম্ভব হচ্ছে- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও নাগরিক সাংবাদিকতার মাধ্যমে। ২০২০ সালের ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনের কথা বলা যায়- যেখানে সাধারণ মানুষের ধারণকৃত ভিডিও এবং পোস্টগুলি বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলেছিল। ২০২৩ সালে তুরস্কে ভূমিকম্পের সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইন সংবাদ মাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে- যা ট্র্যাডিশনাল মিডিয়ার তুলনায় দ্রুত সংবাদ পরিবেশন করেছে।
প্রযুক্তির বিকাশের ফলে সাংবাদিকতা এখন আর শুধুমাত্র প্রিণ্ট ও টিভি মিডিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। অনলাইন নিউজ পোর্টাল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ব্লগিং সাংবাদিকতাকে নতুন রূপ দিয়েছে। বিশ্বখ্যাত নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং দ্য গার্ডিয়ান-এর মতো ঐতিহ্যবাহী সংবাদমাধ্যমগুলো ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশনের দিকে ঝুঁকছে। দেশের প্রিণ্ট মিডিয়াগুলোও প্রিণ্ট ভার্সনের পাশাপাশি ভিডিও কনটেণ্ট প্রকাশ ও প্রচার করছে। এক্ষেত্রে প্রথম আলো ও বিবিসি বাংলা অনলাইনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। একই কারণে নাগরিক সাংবাদিকতা নামে একটি বিষয় সামনে চলে এসেছে। ইচ্ছে করলেও এখন আর নাগরিক সাংবাদিকতাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার উপায় নেই। সাধারণ মানুষ এখন স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে খবর সংগ্রহ ও প্রচার করতে পারছে। বিভিন্ন আন্দোলন ও বিক্ষোভের সময় সাধারণ মানুষ সরাসরি লাইভ স্ট্রিমিং ও ছবি প্রকাশ করছে- যা মূলধারার মিডিয়ায়ও গুরুত্ব পাচ্ছে। এটি গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে।
অন্যদিকে, সাংবাদিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী পেশা হলেও এর সামনে বহু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ডিজিটাল সাংবাদিকতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ভুয়া খবরের (Fake News) প্রসারও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। তাই ফ্যাক্ট-চেকিং এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভুয়া ও মিথ্যা সংবাদ সমাজে এক বিপজ্জনক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এই ধরনের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজে গুজব, বিভ্রান্তি এবং আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো ভুয়া সংবাদের কারণে জাতিগত দাঙ্গা, ধর্মীয় সহিংসতা কিংবা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়- যা মানুষের জীবন ও সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। গত বছরের ৫ আগস্টের পর যে ‘মব জাস্টিজ’ হয়েছে- তার নেপথ্যেও ভুয়া খবর অনেকাংশে দায়ী।
মিথ্যা সংবাদ মানুষের চিন্তা ও মতামতকে প্রভাবিত করে। অনেক সময় মানুষ ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে তরুণ সমাজ এই সংবাদের শিকার হয়ে ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। এছাড়া গণমাধ্যমের প্রতি মানুষের বিশ্বাস কমে যায়, গণমাধ্যমের নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়- যা গণতন্ত্র ও সত্য প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
ভুয়া সংবাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচতে প্রয়োজন সচেতনতা, সঠিক তথ্য যাচাই এবং দায়িত্বশীল গণমাধ্যম চর্চা। মিথ্যা সংবাদ প্রচার ও শেয়ার করা থেকে বিরত থাকাই একজন সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব। সত্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্যই সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে পারে। ভুয়া, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ যাচাই করতে বর্তমানে ফ্যাক্টচেক.বিডি, অল্টনিউজ, ‘Full Fact’ বা ‘Snopes’ -এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো কাজ করছে।
তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তারের ফলে তথ্যের প্রবাহ যেমন দ্রুত হয়েছে, তেমনি ভুল বা মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর হারও বেড়েছে। সাংবাদিকদের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো স্বাধীন সাংবাদিকতার সংকট। অনেক দেশে রাজনৈতিক চাপ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং কর্পোরেট স্বার্থ সাংবাদিকতার স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ফেলছে। সাংবাদিকরা অনেক সময় সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে হয়রানি, মামলা, এমনকি সহিংস হামলারও শিকার হচ্ছেন। অনেক দেশে সাংবাদিকদের ওপর রাজনৈতিক প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়, এমনকি তাঁদের গ্রেপ্তার বা হত্যার ঘটনাও ঘটে। যেমন সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগির হত্যা, বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা ইত্যাদি।
অর্থনৈতিক দিক থেকেও সাংবাদিকতা বড় চাপে রয়েছে। বিজ্ঞাপনভিত্তিক আয়ের মডেল ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞাপনদাতারা সোশ্যাল মিডিয়া ও গুগলের দিকে ঝুঁঁকছেন- ফলে প্রচলিত মিডিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান কর্মী ছাঁটাই করছে বা বেতন কমাচ্ছে- ফলে মানসম্পন্ন প্রতিবেদন তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এছাড়া ‘সেন্সেশনালিজম’ বা চটকদার শিরোনামের প্রবণতা ও ক্লিকবেইট সাংবাদিকতা পেশার নৈতিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। অনেক সাংবাদিক এই চাপে পড়ে প্রকৃত খবরের চেয়ে জনআকর্ষণ তৈরির দিকে বেশি মনোযোগী হচ্ছেন। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা, নৈতিকতা ও স্বাধীনতা রক্ষা এবং প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার।
আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সাংবাদিকতা পেশায়ও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence) আজকের সাংবাদিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবাদ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং পাঠকের কাছে সংবাদ উপস্থাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
প্রথমত, সংবাদ বিবরণী তৈরিতে এআই এর ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP) ২০১৪ সাল থেকেই এআই ব্যবহার করে অটোমেটেড রিপোর্ট তৈরি করছে। প্রতি ত্রৈমাসিকে প্রায় ৪,৪০০টি আর্থিক প্রতিবেদন এআই এর মাধ্যমে তৈরি হয়- যা পূর্বে সাংবাদিকরা হাতে করতেন। এ ধরনের ‘ন্যারেটিভ সায়েন্স’ বা ‘অটোমেটেড জার্নালিজম’ সফটওয়্যারগুলো বিভিন্ন ডেটা সংগ্রহ করে তা থেকে নির্র্ভুুল ও দ্রুত সংবাদ বিবরণী তৈরি করতে সক্ষম।
দ্বিতীয়ত, ভুয়া সংবাদ শনাক্তে এআই একটি বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়া বা অনলাইন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভুল তথ্য ও গুজব চিহ্নিত করতে এখন এআই নির্ভর টুল ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ‘Full Fact’ বা ‘Snopes’ এর মতো ফ্যাক্ট-চেকিং প্ল্যাটফর্মগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করতে এআই ব্যবহার করছে। ২০২২ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, এআই-চালিত ফ্যাক্ট-চেকিং টুলগুলো ৭০% এর বেশি ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ভুল তথ্য চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে।
তৃতীয়ত, পাঠকের পছন্দ ও আচরণ বিশ্লেষণে এআই ব্যবহার করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম পাঠকের আচরণ বুঝে কনটেণ্ট সাজিয়ে দিচ্ছে। যেমন, বিবিসি বা নিউ ইয়র্ক টাইমস এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো পাঠকের পছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তিকৃত নিউজ ফিড তৈরি করতে এআই ব্যবহার করছে। এর ফলে পাঠকের সঙ্গে সংযোগ বাড়ছে এবং এনগেজমেন্টের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
চতুর্থত, ভাষান্তর ও ভাষাগত অন্তরায় দূরীকরণেও এআই এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। Google Translate বা DeepL- এর মতো এআই টুল সাংবাদিকদের এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় দ্রুত ও নির্ভুুলভাবে অনুবাদ করতে সাহায্য করছে। এতে আন্তর্জাতিক খবর সহজেই স্থানীয় ভাষায় উপস্থাপন করা যাচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, Reuters Institute- এর ২০২৩ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রায় ৭৭% সংবাদমাধ্যম কোনো না কোনোভাবে বিশেষ করে সংবাদ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, শিরোনাম তৈরি এবং পাঠকের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণে এআই ব্যবহার করছে।
তবে, এআই ব্যবহারে কিছু চ্যালেঞ্জ ও উদ্বেগও রয়েছে। যেমন, সম্পূর্ণ অটোমেটেড নিউজে মানবিক সংবেদনশীলতা অনুপস্থিত ও সাংবাদিকতার মৌলিক নীতিমালার ব্যত্যয় থাকতে পারে। আবার ভুয়া বা পক্ষপাতদুষ্ট তথ্য থাকলে তা প্রক্রিয়ায় ভুল প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে।
এদিকে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা না থাকলে মূলত: সাংবাদিকতাই থাকেনা। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কেবল ঘটনাকে উপস্থাপন করে না বরং ঘটনার পেছনের কারণ, অনিয়ম, দুর্নীতি ও অপরাধকে জনসমক্ষে আনার চেষ্টা করে। বর্তমান বিশ্বে গণমাধ্যমের গুরুত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রসারও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে আরও সহজ ও কার্যকর করে তুলেছে। বিভিন্ন অনলাইন ডেটাবেইস, সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তিনির্ভর সরঞ্জাম অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য তথ্য সংগ্রহের নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা মূলত: সমাজের আয়না হিসেবে কাজ করে। এটি জনগণকে সচেতন করে তোলে এবং প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তার অপকর্ম, স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম, শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্বলতা কিংবা পরিবেশগত বিপর্যয় সব ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে কিছু সাহসী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন স্বাস্থ্য খাত ও ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম উন্মোচন করেছে- যা প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছে। তবে এই সাংবাদিকতা সহজ নয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের নানা রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। তথ্যপ্রাপ্তির বাধা, আইনি চাপ, হুমকি, এমনকি জীবননাশের আশঙ্কাও থাকে। অনেক সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থামিয়ে দিতে নানা অপচেষ্টা চালায়। তবু সাহসী সাংবাদিকরা থেমে থাকেন না। তাঁদের কাজই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেমন- Panama Papers বা Paradise Papers রিপোর্টগুলো বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তেমনি স্থানীয় পর্যায়ে নানা দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা রিপোর্টগুলোও গণমানুষের মাঝে সচেতনতা ছড়িয়েছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রসার একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এটি ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং মানুষের অধিকার আদায়ে অবদান রাখে। প্রযুক্তি ও জনসচেতনতার সমন্বয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আরও উজ্জ্বল হবে বলেই আশা করা যায়।
সাংবাদিকতার সমসাময়িক চিত্র একটি পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র, যেখানে চ্যালেঞ্জ যেমন রয়েছে, তেমনি সম্ভাবনার দুয়ারও উন্মুক্ত। বর্তমানে দেশ-বিদেশের সাংবাদিকতা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও প্রযুক্তি, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং বিকল্প আয়ের মডেলগুলো এর সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করছে। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রসার এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উপর জোর দিয়ে ভবিষ্যতে আরও উন্নত সাংবাদিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব। ভবিষ্যতে সাংবাদিকতা আরও স্বাধীন, প্রযুক্তি-নির্ভর এবং পাঠক-কেন্দ্রিক হয়ে উঠবে- এটাই প্রত্যাশা।
লেখক: মু. জোবায়েদ মল্লিক বুলবুল ॥ সাংবাদিক ও কলামিষ্ট